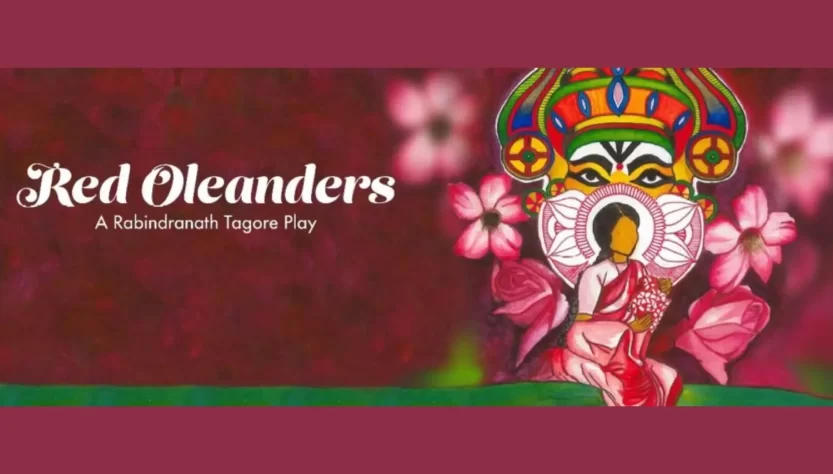শিলং-এর শৈলবাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি রূপক-সাংকেতিক নাটক লেখেন, নাম ছিল ‘যক্ষপুরী’৷ সেটা ১৯২৪ সাল, বাংলাতেই লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ‘যক্ষপুরী’ শিরোনামের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ নাম দেন, নাটকটি যখন প্রবাসীতে প্রকাশ হয়৷ ১৯২৫ সালে ‘Red Oleanders’ নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে নাটকটি তর্জমা করে প্রকাশ করেন৷ সেই হিসেবে রক্তকরবী নাটকটির এবছর শতবর্ষ পেরলো।
মানুষের অসীম লোভ কীভাবে জীবনের সব সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অগ্রাহ্য করে মানুষকে নিছক যন্ত্র ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করেছে৷ ফলে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ, প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকটিতে৷ নাটকের মুখ্য চরিত্র ‘নন্দিনী’, তার মুখোমুখি শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রগুলির গল্পের মাধ্যমে নিপীড়ন, মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামের বিষয়বস্তু সামনে আসে ও মুখোমুখি হয়, যা খুবই প্রাসঙ্গিক ও সমকালীনও৷ যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ, তার অর্থলোভ দুর্দম৷ লোভের আগুনে পুড়ে মরে সোনার খনির কুলিরা, তারা যেন মানুষ নয় যন্ত্র মাত্র৷ তারা যেন যন্ত্রকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র৷ মানুষ হিসেবে কোনও মূল্য নেই তাদের৷ যন্ত্রবন্ধনে মনুষ্যত্ব, মানবতা পীড়িত ও অবমানিত৷ রবীন্দ্রনাথ ‘নন্দিনী’কে নির্মাণ করেছেন এক সহজ, সৌন্দর্য ও আনন্দস্পর্শের প্রতীক হিসেবে৷ যে সহজতা আমাদের জীবন থেকে চলে গিয়েছে৷ এর জন্য আমাদের অনুশীলন প্রয়োজন৷ বেঁচে থাকার জন্যে৷ ‘নন্দিনী’ অন্ধকারের মাঝে এক আলোক শিখা৷

‘রক্তকরবী’ নাটকটি বিভিন্ন সময়ে নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যদল বহুরূপীর প্রযোজনায় ১৯৫৪ সালের ১০ই মে কলকাতায় রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউটে প্রথম মঞ্চ পরিবেশনা হয়েছিল নাটকটির৷ যা বাংলার নাট্য ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠে৷ শম্ভু মিত্রের উদ্ভাবনী ও সামাজিক সচেতনার প্রতিফলন ছিল রক্তকরবী’র নাট্যরূপটিতে। নন্দিনীর রূপদানে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র৷ খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ নৈপুণ্য এবং তাপস সেনের আলোর কারুকৃৎ ছিল উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণের দলিল৷ জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একবারই জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়িতে বাড়ির সদস্যরা মিলে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন৷ বহুরূপীর নাট্যরূপে ছোটখাটো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রক্তকরবী মঞ্চস্থ হয়েছিল, সংলাপের দৈর্ঘ্য কমানো বা কিছু গান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েও সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল। এবং অবশ্যই নাটকের মান অক্ষুণ্ণ রেখে৷ তাই তো সকলে বলতেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকটি লিখেছিলেন এবং শম্ভু মিত্র নাটকটির ধারণা দিযেছিলেন দর্শকদের সামনে৷ তিনি যেন নাটকটির পালকপিতা হয়ে উঠেছিলেন৷ বহুরূপীর প্রযোজনায় নাটকটি বহু জায়গায়, বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। তার রেকর্ডও আছে৷
১৯৮৭ সালে কুমার রায়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মঞ্চস্থ হয় ‘রক্তকরবী’ বিশ্ববিদ্যালয়েই৷ দেবেশ রায়চৌধুরী রাজার ভূমিকায় এবং নন্দিনীর চরিত্রে ছিলেন মঞ্জু চক্রবর্তী৷ সেবছর রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময়ই রক্তকরবী প্রদর্শিত হয়, প্রত্যেকেই খুবই ভালো অভিনয় করেন৷ কবি পক্ষে কোন বিভাগ কত ভালো অনুষ্ঠান করছে সেই নিয়ে এক সুস্থ প্রতিযোগিতাও থাকত তলে তলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে৷কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের উপস্থাপনা খুবই উন্নত মানের হত৷ তখন রক্তকরবী নাটকের গান সবার মুখে মুখে ঘুরত। এতটাই ছাপ ফেলেছিল নাটকটি।

২০১০ সালে দেখলাম রক্তকরবী দেখলাম নৃত্যনাট্য রূপে৷ জাহ্নবী-এর প্রযোজনায়, রাজা – মনোজ মুরলী নায়ার এবং নন্দিনীর ভূমিকায় মধুবনী চট্টোপাধ্যায়৷ মঞ্চসজ্জা করেছিল সঞ্চয়ন ঘোষ৷ রাজাকে পরানো হয়েছিল শাস্ত্রীয় নৃত্য কথাকলির পোশাক৷ অন্য রূপে ‘রক্তকরবী’ মঞ্চে সেই প্রথমই নৃত্যে ও নাট্যে রক্তকরবী৷ মনোজ মুরলী নায়ারকে পাওয়া গেল অন্য রূপে, অন্য অন্বেষণে। কথাকলি শৈলীতে মনোজ আর মধুবনীর নন্দিনীর প্রকাশ পেযেছিল ভরতনাট্যমে৷ নিঃসন্দেহে সাহসী প্রযোজনা, যেহেতু নৃত্যনাট্যের রূপরেখায় ভরে উঠেছিল মঞ্চ ও দর্শক মন৷ রাজাকে আড়ালের ব্যবধান থেকে প্রকাশ্য সমাবেশেই এনেছিলেন নির্দেশিকা মধুবনী চট্টোপাধ্যায়৷ নৃত্যনাট্যে ‘রক্তকরবী’ মঞ্চানুযায়ী রূপটান দেওয়া অত সহজ নয়, কিন্তু প্রযোজনার গুণে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল সফলভাবেই৷
পায়ে পায়ে ‘রক্তকরবী’ শতবর্ষের আঙিনা পেরিয়েছে। অনেক নাট্যগোষ্ঠী নানা ভাবনায় মঞ্চস্থ করেছে৷রবীন্দ্রনাথ এত আধুনিক ও সমকালীন ভাবনায় নাটকটি লিখেছিলেন, যা বিশ্বব্যাপী সমকালীন৷ মনুষ্য সভ্যতায় যন্ত্র প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বা দিল— এটাই যান্ত্রিকতার ধর্ম এবং কবি তা বিশ্বাস করেই তুলে ধরেছেন৷ নন্দিনীর প্রেমাস্পদ যান্ত্রিকতার যুপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হ’ল৷ বিশ্ব সংসারে মানুষের শোষণ, প্রতিবাদ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরতে পরতে দেখা যাচ্ছে৷ নাটকের চরিত্রগুলো যেন এক একটি প্রতীক৷ রাজা, সর্দার, নন্দিনী, রঞ্জন, বিশু, অধ্যাপক, ফাগুলাল৷ রঞ্জন যেমন নন্দিনীর প্রেমিক, রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক— আবার রাজার চরিত্রটি লোভী, অত্যাচারী, প্রজাশোষণে বিশ্বাসী, নিজের শক্তির অহংকারে নিজেকেই বন্দি করে রেখেছে৷ বন্দিত্ব থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে শুধু নন্দিনী৷ রঞ্জন মুক্তির অনুপ্রেরণা আর রক্তকরবী মুক্তির প্রতীক৷ রঞ্জনের ভালবাসার রঙ রাঙা তাই তো নন্দিনী গলায়, কানে, হাতে, বুকে পরে থাকে রঞ্জনের আদরের ডাক রক্তকরবীকে৷ রঞ্জনের মৃতদেহ রাজার ঘরে দেখা নন্দিনীর জীবনে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি৷ কিন্তু নন্দিনী ভেঙে না পড়ে বেছে নেয় প্রতিরোধের পথ৷

সন্দর্ভ নাট্যদলের প্রযোজনায় ২০১৬ সালে ‘রক্তকরবী’ অন্যরূপে দেখা যায়, সম্পাদনা ও নির্দেশনায় গৌতম হালদার এবং নন্দিনীর চরিত্রায়নে ছিলেন চৈতী ঘোষাল৷ অধ্যাপকের ভূমিকায় আলোকচিত্রী অশোক মজুমদারকে নতুন ভাবে দেখা যায়৷ সরোদে ও গানে উস্তাদ আমজাদ আলি খান, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, উস্তাদ রাশিদ খান, আমান আলি খান, আয়ান আলি খান এবং কৌশিকী চক্রবর্তী। প্রত্যেকের সুর যাদুর মাধুর্য্য এক অন্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে৷ চৈতি ঘোষালের নন্দিনী অবশ্যই রেখাপাত করে অভিনয়ের বৈভবে৷ অশোক মজুমদারের অধ্যাপক এক নতুন অন্বেষণ নির্দেশকের, এ কথা বলাই বাহুল্য৷ নৃত্য পরিকল্পনাও ছিল যথোচিত৷
ব্রততী পরম্পরা নিবেদন করে রক্তকরবী এক অন্য আদলে৷ মঞ্চে বিভিন্ন ভাবে বসে সব চরিত্র, বেশভূষা চরিত্রানুযায়ী৷ রাজার চরিত্রে দেবেশ রায় চৌধুরী, বিশু পাগলের চরিত্রে শ্রীকান্ত আচার্য্য, নন্দিনীর ভূমিকায় ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ভাবনা ও রূপায়ণে ব্রততী৷ সঙ্গীত পরিচালনা মনোজ মুরলী নায়ার, নৃত্য নির্মিতি, পোশাক পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় মধুবনী চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত আয়োজনে কল্যাণ সেন বরাট খুবই মনোগ্রাহী উপস্থাপনার স্বাক্ষর রাখেন৷ মঞ্চ ভাবনায় তরুণকান্তি বারিক, আলো ও মঞ্চ নির্মাণ দীপঙ্কর দে,সঙ্গীতে মনীষা মুরলী নায়ার এবং ‘ডাকঘর’ প্রত্যেকেই সুগ্রথিত৷

সম্প্রতি ভবানীপুর ‘শিশিক্ষু’ নাট্যদলের প্রযোজনায় চৈতি ঘোষালের পরিচালনায় নতুন রূপে উপস্থাপিত হল ‘রক্তকরবী’ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ৷ নন্দিনী রূপে চৈতি ঘোষাল, রাজা – দেবেশ রায় চৌধুরী এবং অধ্যাপক – অশোক মজুমদার৷ বেশ কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমেই মঞ্চস্থ করেছেন পরিচালক৷ গৌতম হালদার যেমন রাশিদ খানের আলাপের সুরে নিবন্ধ ও বেঁধেছিলেন রক্তকরবীর প্রারম্ভে। এখানে চৈতি রেখেছেন ভাষ্যপাঠে বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের কণ্ঠস্বর৷ দেবজ্যোতি মিশ্রের আবহ যেন একটু বেশি উচ্চকিত লাগছিল। কারণ সংলাপ ছাপিয়ে যন্ত্রের সুর তখন যন্ত্রণার৷ নৃত্য পরিকল্পনায় সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য পরিশীলিত রবীন্দ্রনৃত্যের প্রয়োগ করলে ভালো লাগত৷ রবীন্দ্রনৃত্যের প্রয়োগ ছিল অসাড়৷ ভালো লাগে সৌমেন চক্রবর্তীর আলোর প্রক্ষেপণ ও মঞ্চ নির্মাণ৷ প্রত্যেকেই চরিত্রানুযায়ী যথাযথ৷ অভিনয়, সম্পাদনা ও পরিচালনায় চৈতি ঘোষাল এবং সহযোগী পরিচালক অমর্ত্য রায় ও মিতালি রুদ্র৷ এখনকার বাতাবরণের আভাস অবশ্যই প্রতিফলিত হয় নাটকে৷

রক্তকরবী’র শতবর্ষের পরও আধুনিক সমাজ চিত্র যেন একই রয়ে গেছে৷ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ‘প্রবাসী’ পত্রিকার বৈশাখী সংখ্যায় লিখেছিলেন– ‘রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি ‘নন্দিনী’ বলে একটি মানবীর ছবি৷ চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ৷’ এখানে চৈতি সেটা হাজির করেছেন, রঞ্জনের কথা বলতে গিয়ে যেমন আপ্লুত হয়েছেন, বিশুর সঙ্গে মরমি সম্পর্কের আবার সর্দারের সঙ্গেও যেন তার ভাবের সম্পর্ক৷ নন্দিনী এমনই। যার হৃদয়ে কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই৷ প্রতিরোধ আছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াইকে আহ্বান করে নন্দিনী; রাজা বলে– আমার সঙ্গে লড়াই করবে, তোমাকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি। নন্দিনী বলে– আমার সেই মরা তোমাকে মারবে৷ আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু৷ এখানে নন্দিনীরূপী চৈতির অস্ত্র অভিনয়, সাবলীল অভিনয়৷ কবি যেন নাটকটিতে জড় যান্ত্রিকতা ও জীবনধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন৷ চৈতিও রক্তকরবীর মতো সাংকেতিক নাটকের মধ্যে- মৃত্যু কোনও পতন নয় বরং ভিন্ন ব্যঞ্জনায় রঞ্জিত দেখিয়েছেন৷ মঞ্চে এক শিশুর আবির্ভাব ও রাজার স্বহস্তে ধ্বজা ভেঙে ফেলা– সবই যেন মানবতার মুক্তি৷ এখনকার সমাজ চিত্র, যে বিচিত্র স্রোত বইছে, তার সঙ্গে যেন সাযুজ্যতা পাই নাটকে, পরিচালকও মিলিয়েছেন৷ তাই রক্তকরবী শতবর্ষ পেরিয়েও এখনও প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন৷